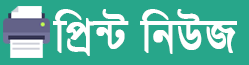
বাংলাদেশ সময়ের এক চমৎকার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। যেখানে তরুণ প্রজন্ম শুধু জনসংখ্যার বড় অংশ নয়, সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের কাণ্ডারি। তবে তরুণদের যে স্বপ্ন, সম্ভাবনা ও বাস্তবতা, তার মধ্যে এখনও বিস্তর ব্যবধান রয়েছে।
শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা বা কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। তাদের ঠিক করতে হবে তারা কী হতে চায়। দেশ ও সমাজের ভবিষ্যতের পাশাপাশি নিজেদের ভবিষ্যৎও ঠিক করে স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।
জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী, আগামী ২০৩৭-৩৮ সাল পর্যন্ত জনমিতিক লভ্যাংশের সুফল ভোগ করবে বাংলাদেশ। এ সময় পর্যন্ত দেশের জনসংখ্যার বেশির ভাগই কর্মক্ষম থাকবে। এ ক্ষেত্রে জাতীয় সাফল্য অর্জনে তরুণদের সার্বিক ক্ষমতায়নে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে এই তরুণেরা একসময় দেশের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ছাত্ররা অসাধ্যকে সাধন করেছে। যেভাবে আন্দোলন করে তারা গর্বিত ইতিহাসের অংশ হয়েছে, সে রকম মনোযোগ, পরিশ্রম দিয়ে নিজ নিজ পেশা, ব্যবসা বা পড়াশোনায় উন্নতি লাভ করতে হবে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের আন্দোলনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবতার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকলে তা থেকে হতাশার জন্ম নিতে পারে। দেশের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধিতে তরুণদের জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তরুণদের মধ্যে যে অপার সম্ভাবনা আমরা দেখি, এটি বাস্তবে রূপ দিতে চারটি মূল স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে– কর্মসংস্থান, জনসম্পদে রূপান্তর প্রক্রিয়া, আত্মনির্ভরতা ও মানসিক স্বাস্থ্য। এই চারটি স্তম্ভে যদি সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বিনিয়োগ না হয়, তবে এ প্রজন্মের সম্ভাবনা আটকে থাকবে শুধু তথ্য-উপাত্তে।
দেশের তরুণদের জন্য স্থায়ী ও সম্মানজনক কর্মসংস্থান এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। চাকরি শুধু অর্থ উপার্জনের মাধ্যম নয়, এটি তাদের আত্মপরিচয় ও মর্যাদার প্রতীক। অথচ আমরা এমন বাস্তবতার মুখোমুখি, যেখানে উচ্চশিক্ষিত তরুণদের বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। প্রতি ১০০ জন বেকারের মধ্যে ২৮ জন উচ্চশিক্ষিত। বৈষম্যহীন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কৌশল প্রণয়ন ও পুনর্নির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণবিষয়ক টাস্কফোর্সের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।
এর মানে, সমস্যাটি শুধু চাকরির অপ্রতুলতার কারণে নয়; আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শ্রমবাজারের মেলবন্ধনের অভাবও এর পেছনে দায়ী। বর্তমানে নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা শুধু সনদ নয়; প্রযুক্তিগত দক্ষতা, বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এখনও শ্রমবাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন পূরণ করতে হলে শিক্ষা, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি, ফাইন্যান্স, লজিস্টিকস, পুনঃনবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সফট স্কিলসের ওপর জোর দিতে হবে।
অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সে অনেক শিক্ষার্থী দেখেছি, যারা থিওরি জানে কিন্তু বাজেট বানাতে জানে না, বিনিয়োগ নিয়ে তাদের প্রাথমিক ধারণা নেই, এমনকি ব্যাংকিং অ্যাপ ব্যবহারেও তারা দ্বিধাগ্রস্ত। অথচ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার অন্যতম চাবিকাঠি হলো আর্থিক সচেতনতা, যা এখনও আমাদের মূলধারার শিক্ষায় অনুপস্থিত।
বিশ্বের উদীয়মান অর্থনীতি ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনসহ অনেক দেশে স্কুল থেকেই আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ে শেখানো হচ্ছে। আমাদেরও উচিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব, সঞ্চয়, বিনিয়োগ এবং মৌলিক ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা যুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ভার্চুয়াল ট্রেডিং সিমুলেশন প্রোগ্রাম ও ক্যাম্পাসে বিনিয়োগ ক্লাবের মতো উদ্যোগ তরুণদের মধ্যে আর্থিক সক্ষমতা ও আগাম সচেতনতা তৈরিতে ভূমিকা রাখবে।
এর পাশাপাশি একটি বড় সম্ভাবনার নাম হচ্ছে উদ্যোক্তা তৈরি। বর্তমানে তরুণদের মাঝে আত্মকর্মসংস্থানের চেতনা বাড়ছে। তরুণদের অনেকে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন ব্র্যান্ড তৈরি করছে, গ্রামীণ এলাকায় ই-কমার্স চালু করছে কিংবা তথ্যপ্রযুক্তিগত সেবা এক্সপোর্ট করছে। এসব উদ্যোগে সবচেয়ে বড় মূলধন হলো নিজের দক্ষতা। আমাদের তরুণদের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম রয়েছে। নতুন দক্ষতা অর্জনেও তারা ইচ্ছুক। কিন্তু নতুন উদ্যোগ গ্রহণে তারা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়; যেমন– জটিল নিবন্ধন প্রক্রিয়া, সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণের অভাব এবং ব্যবসায়ে সময়োপযোগী ও ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরামর্শ পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সংকট। এ ধরনের প্রতিবন্ধকতার ফলে সম্ভাবনাময় বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হচ্ছে, আবার তরুণদের উদ্যোগ গ্রহণের প্রবণতাও নিম্নমুখী হচ্ছে।
বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে উদ্যোক্তা হওয়ার হার দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় নিচে। ২০২৩ সালে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) একটি জরিপে উঠে এসেছে, ৬৮ শতাংশ তরুণ উদ্যোক্তা অর্থ সংকটকে তাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করে। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক ইনকিউবেশন সেন্টার, স্টার্টআপ ল্যাব ও সরকারি সহায়তায় ‘সিড মানি’ প্রকল্প। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি তা প্রান্তিক পর্যায়েও বাস্তবায়ন করতে হবে। ঢাকার বাইরেও যেন বরিশাল, কুমিল্লা বা সৈয়দপুরের তরুণ উদ্যোক্তারা অ্যাকসেলেরেটর সাপোর্ট পান, তা নিশ্চিত করতে হবে।
তবে শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো বা উদ্যোক্তা তৈরি করলেই চলবে না, পাশাপাশি আমাদের তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথাও ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে, তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশেও একটি সহানুভূতিশীল পরিবেশ দরকার। গত বছর প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে উঠে আসে, দেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ২৫ থেকে ৭১ শতাংশ মধ্যম থেকে তীব্র বিষণ্নতা, উদ্বেগ বা মানসিক চাপের সম্মুখীন। সম্প্রতি প্রকাশিত আঁচল ফাউন্ডেশনের এক জরিপে জানা গেছে, ১৩ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে আত্মহত্যার হার সবচেয়ে বেশি। এর পরেই রয়েছে ২০ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা (২৪ শতাংশ)।
শিক্ষার্থীরা কোনো না কোনো ধরনের মানসিক চাপে থাকলেও এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য বড় পরিসরে সহায়তামূলক উদ্যোগের বাস্তবায়ন নেই। এ সমস্যা মোকাবিলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এখন ‘মানবিক শিক্ষায়তন’-এ পরিণত হতে হবে, যেখানে শুধু গ্রেড নয়; বরং আবেগ, সহানুভূতি ও মননচর্চাকেও অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
তরুণদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন সামাজিক-নাগরিক ক্ষেত্রেও। শুধু ভোট দেওয়া নয়; বরং পরিবেশ, লিঙ্গসমতা, প্রযুক্তি শিক্ষা, এমনকি স্থানীয় সরকারেও তাদের মতামত ও অংশগ্রহণ জরুরি। তরুণদের নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন প্রয়াস ইতোমধ্যে আমরা দেখছি, যেমন জলবায়ু আন্দোলন, নারী অধিকারে প্ল্যাটফর্ম অথবা প্রান্তিক জনগণের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা প্রভৃতি। এ উদ্যোগগুলোর পেছনে যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তা প্রশংসার যোগ্য। এখন দরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে তরুণদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং তাদের সঙ্গে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের সংযোগ তৈরি করা।
এসব উদ্যোগ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে একা করা সম্ভব না। এ জন্য চাই সমন্বিত কৌশল, একটি জাতীয় রূপরেখা; যেখানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, আইসিটি বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রবাসী পেশাজীবীরা একসঙ্গে কাজ করবেন।
আমাদের সম্ভাবনাময় তরুণ রয়েছে, কিন্তু তাদের মেধার পূর্ণ বিকাশের জন্য যে কাঠামো দরকার, তা এখনও আমরা সম্পূর্ণভাবে তৈরি করতে পারিনি। ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ শুধু সুযোগই নয়, দায়বদ্ধতাও। আমরা যদি এখন সেই দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হই, ভবিষ্যৎ আমাদেরই দায়ী করবে। তারা চিন্তায় স্বাধীন এবং স্বপ্নপূরণে উদ্যমী। তাদের সুযোগ আর সঠিক কাঠামোর অভাব। আমাদের এখন সেই সুযোগ তৈরি করতে হবে, কাঠামো গড়ে তুলতে হবে; যেখানে নীতিগত আচরণ, শিক্ষাব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং মানসিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
লেখক-সহকারী অধ্যাপক, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ
siahmed@aiub.edu








